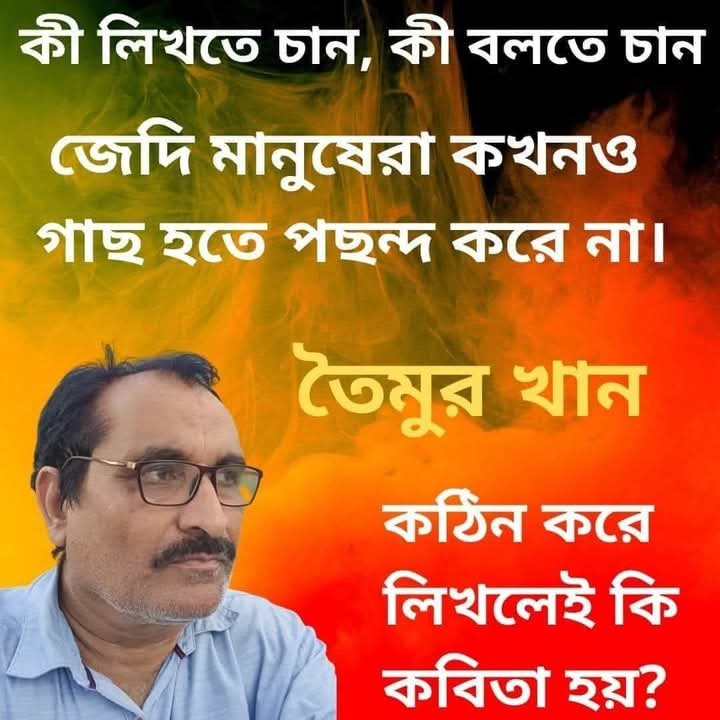কবিতার পাঠক এবং পাঠকের কবিতা
তৈমুর খান
--------------------------------------------------------------------
আবেগ যখন চিন্তা খুঁজে পায়, চিন্তা যখন শব্দ খুঁজে পায়, কবিতা তখন সহজ অনবদ্য আবেদনেই পাঠককে নাড়া দেয়। এই পাঠকই তখন প্রকৃত কবিতা খুঁজে পান,এই কবিতাই তখন প্রকৃত পাঠক খুঁজে পায়। দুইয়েরই যুগপৎ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর কখনও ছেদ পড়ে না।
প্লেটো বলেছিলেন:
“Beauty of style and harmony and grace and good rhythm depend on simplicity.”
অর্থাৎ শৈলীর সৌন্দর্য এবং সাদৃশ্য এবং করুণা এবং ভালো ছন্দ সরলতার উপর নির্ভর করে।
কথাটি মনে এলো বেশ কিছুদিন থেকেই কিছু কবির কবিতা পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগছে: এগুলি কি কবিতা? কঠিন করে লিখলেই কি কবিতা হয়? ঘুরিয়ে পেচিয়ে জবরজং শব্দের আড়ালে নিজের ভাবকে কি প্রতিস্থাপন করা যায়? উপলব্ধির বা অনুভূতির সূক্ষ্ম মোচড় সেগুলোতে খুঁজে পাই না। তার বদলে বরং এক কৃত্রিম কারিশমা জাহির করেন কবিরা। কী লিখতে চান, কী বলতে চান, কী তার ছান্দিক চল তার কিছুই খুঁজে পাই না। কবিতায় রহস্যময়তা থাকে। না বলা থাকে। শূন্যতার স্পেস থাকে। নীরবতার গভীর অন্তর্দৃশ্য থাকে। কিন্তু এলেবেলে পরিশ্রমলব্ধ ইট-কাঠ-পাথরের দেয়াল তুলে দুর্বোধ্য নির্মাণ সহজে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ তা শিল্প নয়। পরিশীলিত শিল্পনির্মাণ এবং তার শিল্পের মেকানিজম প্ল্যাটফর্ম তো অনেক সময় বিষয় এবং অর্থের ঊর্ধ্বে আপনা থেকেই মনকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এইসব লেখা পড়তে গিয়ে বারবার বিকর্ষিত ও বিরক্তি বোধ জাগ্রত হচ্ছে। মতামত তো দূরের কথা, পড়ে দেখার ইচ্ছাও জাগে না। সহজ এর মধ্যেই যে সৌন্দর্য থাকে, যে সত্য থাকে, যে অন্তর থাকে তা কি অন্যকিছুর মধ্যে থাকে? এই কারণেই ওয়াল্ট হুইটম্যান বলেছিলেন:“The art of art, the glory of expression, and the sunshine of the light of letters, is simplicity.”
অর্থাৎ শিল্পের শিল্প, প্রকাশের মহিমা এবং অক্ষরের আলোর রোদ, সরলতা।
একথা অনেকেই না মানতে পারেন সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু যাঁদের কবিতা পড়ে বর্তমান প্রজন্ম অনুপ্রেরণা পাবে, বা কবিতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবে এমনটি হয় না। বরং তার বদলে বর্তমান প্রজন্ম বিভ্রান্ত হবেন এবং কবিতার প্রতি বিমুখ হবেন। শুধু ফেসবুক বলেই নয়, আমাদের কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে চিহ্নগুলি বহন করে নিয়ে চলেছি আমরা তা যেন সত্য-সুন্দরের অনুসারী হয়। প্রতিটি কাজেই ফুটে উঠে আমাদের যত্ন ও নিষ্ঠা এবং অন্তরের স্পর্শ এটাই খেয়াল রাখতে হবে। নিজেকে ব্যতিক্রমী করতে গিয়ে আমরা ব্যতিহার করে ফেলছি। শিল্পসাধনা করতে গিয়ে শিল্পহীন হয়ে উঠছি। কবিতা লিখতে গিয়ে ভূরি ভূরি অকবিতার জন্ম দিচ্ছি। যেখানে সারল্য প্রয়োজন, সেখানে বজ্রকঠিন অসুন্দরের আমদানি করছি। ফলে কবিতার প্রাণ হারিয়ে যাচ্ছে। শুধু কঙ্কালসর্বস্ব নির্মাণ এবং কিম্ভূতকিমাকার এক শিল্প প্রসব করে চলেছি। আমাদের কিছু ভক্ত ওরফে অপাঠক আমাদের খুব সুনাম করছে। আসলে তারা যে পাঠকই নয়, তাদের মন্তব্যগুলোও দায়সারা, কবিতা সম্পর্কে তারা যে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী, নতুনত্বকে ধারণ করার ক্ষমতা তাদের যে নেই, এবং সর্বোপরি তাদের প্রশংসা বা গুণগান কবিদের যে কোনো কাজে লাগে না তা বলাই বাহুল্য।
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:
"সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।"
সহজ করে বলা বিশ্বকবির কাছেও সেই সময় কঠিন ছিল। আজকের দিনেও কঠিন। যিনি যত বড় কবি অথবা যত বড় সাধক, তিনি তত সহজ, তত অনন্ত, তত অনপনেয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অন্যান্য মহাপুরুষদের থেকে নিজেকে আলাদা করতে পেরেছিলেন এই সরলতার কারণেই। তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে মাত্র চারটি শব্দই যথেষ্ট ছিল। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন:
"যত মত তত পথ"
এত সহজ করে বলা একজন বড় সাধকেরই পরিচয়। তেমনি কবিদের ক্ষেত্রেও একটা বড় পরিচয় তাঁদের সহজাত সারল্য। বহু ভাব, জীবনের বহুমুখী প্রাচুর্য, শাশ্বত প্রবৃত্তির উন্মোচন, সময়ের গভীর অন্তঃক্ষরণ, যুগের সংকট ও বিস্ময়, শূন্যতা ও নীরবতার নিরবধি স্পেস কয়েকটি শব্দে, কয়েকটি চিত্রকল্পের আঁচড়ে, কয়েকটি ব্যঞ্জনার ইশারায় অথবা না বলা শূন্যতায় তা উচ্চারিত হতে পারে। কবি যখন নিজেকে নিয়ে লেখেন, তখন কবি নিজেও এই সময়ের, এই সমাজের, এই রাষ্ট্রের, এই সভ্যতারই একজন সদস্য। কোনো না কোনোভাবে তিনি বিচ্ছিন্ন থেকেও অবিচ্ছিন্ন। তাঁর জীবন-সংস্কৃতি, আত্মচেতনা, আত্মঅবস্থান সবকিছুই সেখানে এসে উপস্থিত হয়। গোচরে-অগোচরে তিনি তার অনুকার হয়ে ওঠেন। তাই নিয়েই তো কবিতা!
তখন এই সময়ের কবিই লিখতে পারেন:
"তুমি আমাকে মেঘ ডাকবার যে বইটা দিয়েছিলে একদিন
আজ খুলতেই দেখি তার মধ্যে এক কোমর জল।
পরের পাতায় গিয়ে সে এক নদীর অংশ হয়ে দূরে বেঁকে
গেছে।
আমাকে তুমি উদ্ভিদ ভরা যে বইটা দিয়েছিলে
আজ সেখানে এক পা-ও এগোনো যাচ্ছে না, এত জঙ্গল।
গাছগুলো এত বড় হয়েছে যে মাটিতে আলো আসতে
দিচ্ছে না।
তুমি আমাকে ঝর্ণা শেখবার যে বইটা দিয়েছিলে
আজ সেখানে মস্ত এক জলপ্রপাত লাফিয়ে পড়ছে
সারাদিন।
এমনকি তোমার দেওয়া পেজ-মার্কের সাদা পালকটাও
যে বইতে রেখেছিলাম, সেখানে আজ
কত সব পাখি উড়ছে, বসছে, সাঁতার কাটছে।
তোমার দেওয়া সব বই এখন মরুভূমি আর পর্বতমালা,
সব বই আজ সূর্য, সব বই দিগন্ত …
অথচ আজকেই যে আমার লাইব্রেরি দেখতে আসছে বন্ধুরা
আমার পড়াশোনা আছে কিনা জানার জন্য! তাদের আমি
কী দেখাবো? তাদের সামনে কোন মুখে দাঁড়াবো আমি!
(প্রেমিক : জয় গোস্বামী)
কবিতার ব্যাখ্যা তখন খুব একটা প্রয়োজন হয় না। উপলব্ধিটাই আমাদের হৃদয়ের উৎস হয়ে যায়। যে গল্পের জন্ম হয় তা আসলে আমাদের একার গল্প নয়। একার ভালো লাগা, একার যাপন, একা প্রেমের স্রোতে ভেসে যাবার, হেসে উঠবার, স্বপ্ন দেখবার, আনন্দে শিহরিত হবার মুহূর্তগুলিও সকলের সব সময়ের জন্যই মর্মরিত হতে বাধ্য। অথচ কবিতাটিতে একটাও কঠিন শব্দ নেই। ঘুরিয়ে পেচিয়ে নাক দেখানো নেই। কষ্টকল্পিত বাহাদুরি নেই। সহজ সাবলীল এক গতি ও অনুভূতির কাল্পনিক প্রক্ষেপণ আছে। পাঠে বিস্মিত হবার ও পুলকিত হবার অবকাশ আছে।
বিভাস রায়চৌধুরী ছন্দোবদ্ধ ভিন্নধর্মী এক কবিতায় সেভাবেই আমাদের টানলেন। কবিতার কিছুটা অংশ এরকমই:
"কখনও আমি শব্দ ভেঙে
মর্ম ছুঁতে যাইনি
চাইনি কিছু পাইনি কিছু
চাইনি, কিছু পাইনি।
এই যে আমি স্বপ্নকামী
জ্বরের ঠোঁটে বিষ।
বীর্যপাত, তরল চাঁদ
দেখছি ভাগ্যিস
কখনো আমি বমির ঝুঁকে
গলন প্রিয় মেম
রাত জেগেছি, সঙ্গী সাদা
বিদায়ী কনডম।
ঘুমাও পাখি, আমার হাতে
চমকপ্রদ পেন।
কাটছি লেখা, হাঁটছি সুখে
সঘন শ্যাম্পেন।
সব বুঝেছি, সব মুছেছি
বুঝলি খোকা খুকু!
খিদের দেশে ল্যাজ বেড়েছে।
ছন্দ, মানে কুকুর
তাই তার টুঁটি কামড়ে ধরে
হিংস্র হয়ে যাই।
একটা-দুটো ফুল এনেছে।
আমারই বনসাই
এই যে আমি বামন, তবু
বাল্য প্রেমে ভরা।
চাঁদ ধরতে পারিনি, তুমি
বকো বসুন্ধরা।
(সমস্ত পাগল আমি)
আত্মগত শূন্যতা আর বঞ্চনাকে সহ্য করেও 'খিদের দেশে ল্যাজ বেড়েছে। ছন্দ, মানে কুকুর' লিখতে পারা শব্দবন্ধে গতানুগতিক প্রকাশ নেই। অন্তর্জ্বালাকে সরাসরি পাবকের প্রজ্জ্বলনে তিনি শিখায়িত করেননি। এমনকী হিংস্র হয়ে যাওয়াতেও বাংলা ভাষা ভীত হয়নি। তেমনি 'বীর্যপাত', 'কনডম', 'শ্যাম্পেন' শব্দগুলি ব্যবহার করাতেও বাংলা ভাষা কলঙ্কিত হয়নি। বরং সুচারু কাব্যিক নিবেদনে তা প্রাখর্য্য পেয়েছে। কবিতার তরঙ্গ আত্মজৈবনিক অভিঘাতে মানবিক প্রশ্রয় পেয়েছে। 'বকো বসুন্ধরা' ব্যবহার করায় তা সময়কে এবং ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করেছে।
শ্রীজাত এই সময়ের আর এক উল্লেখযোগ্য কবি। শুধু ছন্দের জন্য নয়, শুধু অনুপ্রাস আর বিরোধাভাস অলংকারের জন্য নয়, তাঁর মানবমঙ্গলের কাঙ্ক্ষা সভ্যতাগামী প্রাচুর্যে যে ব্যাপ্তি ও নির্মাণের অভিঘাত রচনা করেছে তাতে তিনি অসাধারণ হয়ে উঠেছেন। তাঁর একটি ছোট্ট কবিতা:
"মৃত্যু সেজে দাঁড়িয়ে আছে মুখনিচু এক গুরুত্বহীন গাছ
হাত রাখো তার বুকের কাছে, দেখতে পাবে আলো-গহীন গাছ।
ঘোড়ারা সব মৃত এখন, প্রান্তরে এক চাঁদ দাঁড়িয়ে চুপ…
আমার মতো একলা ঘরে কেউ বুঝি আর শোনে মহীন, গাছ?
রোদ চড়েছেন বাবা’র মতো, দেহাতি মা পাঁচিল সারাদিন
ভাই ধুলো, সে গ্রামকে বেড়ায়… চুপটি থাকে ছোটি বহিন গাছ
মৃত্যু সেজে দাঁড়িয়ে আছে মুখনিচু এক গুরুত্বহীন গাছ
হাত রাখো তার বুকের কাছে, দেখতে পাবে আলো-গহীন গাছ।"
(গাছ)
'গাছ' শব্দটি শুধু গাছের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মৃত্যুর পরিধি হয়ে জীবনদায়ী আলোর মুগ্ধতায় সে আত্মগোপন করে আছে। তারও প্রাণের স্পন্দন আছে। বুক আছে। যেখানে হাত রাখা যায়। 'মহীনের ঘোড়া' অর্থাৎ প্রেমিক ইচ্ছার অবদমিত আবেগেরা মরে গেছে। কিন্তু চাঁদ আছে। চাঁদের জ্যোৎস্না আছে। নীরবতার মাঝে কবি শুধু গাছের কথা ভেবেছেন। বাবা রোদ, মা পাঁচিল, ভাই ধুলো, ছোটি বহিন গাছ, আর কবি? কবি তো প্রেমিক। গাছের কাছে আলো দেখেছেন। সকলেই শাশ্বতকালীন মানবসভ্যতার চরিত্র। সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে মহীনের ঘোড়া নয়, নিরীহ গাছ, সভ্যতার গাছ, ছায়া প্রদানকারী গাছ, ফুল-ফল প্রদানকারী গাছই দরকারি। 'ছোটি বহিন গাছ' শব্দটি স্নেহময়, আবেগসম্ভূত, মানবসম্পর্কীয় চিরন্তনতায় ভাস্বর। কবিতাটির নির্মাণে শব্দ ব্যবহারের জাদুও দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। কবি পরপর লিখেছেন: 'গহীন', 'মহীন','বহিন' এর মতো শব্দগুলি। কবিতাটি এই ভাবেই আলো পেয়েছে। একটি নির্মাণ সহজতর বিনির্মাণে কতটা উত্তরণ দাবি করতে পারে তা পরীক্ষিত।
রুদ্র গোস্বামী তাঁর প্রতিটি কবিতাতেই একটি সহজ আবেদন নিয়ে আসেন। তাঁর ভাষার মধ্যেই এমন এক মানবিক স্পর্শ পাওয়া যায় যার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতিকেও নতুন করে চিনতে শিখি। আমাদের রাগ-বৈরাগ্য অভিমান-ভালোবাসা তাঁর শব্দের জাদুতে আয়নার মতো সামনে দাঁড়ায়। তখন ব্যক্তি আমির প্রাচীর ভেঙে বিশ্ব-আমির দিকে ছুটে যায়। আমাদের বালকসত্তা প্রৌঢ়সত্তা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা চিরন্তনকে চিনতে শিখি। একটি কবিতার কিছুটা অংশে তিনি লিখেছেন:
"প্রেমিক হতে গেলে ঋতু বুঝতে হয়
যেমন কোন ঋতুটার বুক ভরতি বিষ
কোন ঋতুটা ভীষণ একা একা, কোন ঋতুটা প্লাবন
কোন ঋতুতে খুব কৃষ্ণচূড়া ফোটে
ছেলেটা ঋতুই জানে না
ও শুধু দেখে আর চেনে, বুঝতে জানে না।
ছেলেটা কখনো প্রেমিক হতে পারবে না
প্রেমিক হতে গেলে গাছ হতে হয়।
ছায়ার মতো শান্ত হতে হয়।
বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়।
জেদি মানুষেরা কখনও গাছ হতে পছন্দ করে না।
তারা শুধু আকাশ হতে চায়।"
(প্রেমিক হতে গেলে)
কবিতাটিতে অচেনা কোনো শব্দই নেই, ঋতু চেনার কথা আছে। এই ঋতু শুধু সময়ের নয়, আমাদের জীবনেরও ঋতু। আমাদের স্বপ্নেরও ঋতু। আমাদের দুঃখ-দুর্দশারও ঋতু। 'ঋতু' শব্দটি এখানে মহীয়ান হয়ে উঠেছে। আমাদের বেঁচে থাকার পারম্পর্যগুলি প্রেমিক-বাসনায় উদ্বোধিত। তারপর 'গাছ' চরিত্রের মধ্য দিয়ে সর্বংসহ বিশ্বাস অর্জনের এক প্রসন্ন বিধান লাভ করার কথা আছে যা কবিতাটিকে যুগোত্তীর্ণ করেছে। শব্দের জৌলুস দরকার হয়নি। প্রকাশের আলো-আঁধারি স্পেসেরও প্রয়োজন পড়েনি, অথচ এক ভালো লাগা থেকে গেছে। এই কারণেই মার্কিন
জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী, বিশ্বতাত্ত্বিক, লেখক এবং বিজ্ঞান যোগাযোগকারী নিল দেগ্রাসে টাইসন(১৯৫৮) বলেছেন :
“Some of the greatest poetry is revealing to the reader the beauty in something that was so simple you had taken it for granted.”
অর্থাৎ কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা পাঠকের কাছে এমন কিছুর সৌন্দর্য প্রকাশ করছে যা এত সহজ ছিল যে আপনি এটিকে মঞ্জুর করে নিয়েছেন।
প্রকৃত কবিতা পাঠক এমন কিছুর সন্ধান পান এই সব কবিতায় যা তারা আপন করে নিতে বাধ্য হন। এই 'এমন কিছুর' মধ্যে থাকে ভাষার সৌন্দর্য, ভাবের আন্দোলিত আবেগময় স্পর্শ। অন্তঃসলিল ফল্গুর মতোই এক স্রোতের টান, যেখানে চিরন্তন বিশ্বচৈতন্যের তরণী ভাসতে থাকে। পাঠক তরণীর যাত্রী হয়ে ওঠেন। ঠিকানা খুঁজতে থাকেন। কেউ কেউ ঠিকানাও পেয়ে যান। রবার্ট ফ্রস্টের কথায় বলতে হয়:
"Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words."
অর্থাৎ কবিতা হল যখন একটি আবেগ তার চিন্তা খুঁজে পেয়েছে এবং চিন্তা শব্দ খুঁজে পেয়েছে।
লেখক: কবি, ছড়াকার ও প্রাবন্ধিক, কলকাতা।